উল্লাস, যা কবিকে সক্রিয় রাখে এবং একই সাথে পরবর্তী সময়ে কবিকে সীমায়িত করে, তিনি যদি পরিবর্তনে অবিশ্বাসী হন। একজন কবি পরিবর্তিত মূল্যগুলোকে গ্রাহ্য করবেন, এটাই স্বাভাবিক। গ্রাহ্য নাও করতে পারেন। সময়ের ব্যবধানে কবিতার পার্থক্য লক্ষ্য করেন পাঠকেরা, পার্থক্য হয় দৃষ্টিভঙ্গিতে, চেতনা থেকে উৎসারিত নতুন কাব্য ভাষায়। নতুন নতুন বিস্ময় সৃজনে ক্লান্তিহীন কবির দশকীয় বিভাজন ভেঙে যেতে থাকে বারবার। কবিতার ইতিহাস, এর ভাষার ইতিহাস--- একথা সকলে জানেন, সকলে না মানলেও। কবিতার ভাষা কতগুলো দৃশ্য শব্দযুক্ত বাক্যবন্ধের বিচারের মধ্যে আটকে থাকে না। শব্দগুলো বিভিন্ন অবস্থা, বোধ ও চেতনার অণুমাত্র। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ আভিধানিক অর্থমাত্রার সঙ্গে নাও মিলতে পারে। বেশ কিছু পাঠক কবিতার দৃশ্য শব্দগুলোকেই বিচার করেন বলে তাকে হতাশ হতে হয়। ফলে তিনি আর ভিন্ন খোঁজের পথ মাড়ান না। ক্লান্ত পাঠক অন্বেষণ রহিত। তাঁর অতো সময়ও নেই অপর খোঁজের, বাস্তবকে সারাদিন নাড়াচাড়া করার পর। আন্তরিক ও দীক্ষিত পাঠকেরও সমস্যা আছে। তিনিও কমিউনিকেশন গ্যাপের শিকার হতে পারেন। তাঁর অমোঘ ইগো বিভিন্ন কমপ্লেক্সিটি তৈরি করতে পারে।
বিভিন্ন ধারায় লেখা হয় কবিতা, পাঠকও আছেন বিভিন্ন ধারার। বাজারী পত্রিকাগুলোতে কবিতার যে পৃষ্ঠা রাখা থাকে, সেখানে কবিতার বদলে প্রচুর পদ্যপ্রবণতা প্রকাশিত হয়। বহু লিটল ম্যাগাজিনও ওই পথ অনুসরণ করে। বাংলা সাহিত্যের বেশিরভাগ লিটল ম্যাগাজিন সামাজিক-রাষ্ট্রিক এস্টাব্লিশমেন্টের দেখানো ভাষায় সাহিত্য করে। বহু পাঠক, সমালোচক, বুদ্ধিজীবী আজকের সাহিত্য বলতে মাত্র সেগুলোকেই বোঝেন। ফলত, হঠাৎ নতুন ভাবনার ও ভাষার কবিতা দেখলে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বিরক্তি প্রকাশ করেন। বহু লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরও একই দশা। তাঁদের নতুন নতুন ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সৃজন সক্রিয়তার ইচ্ছা থাকে না। অনেক লিটল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠাতেও প্রচুর পদ্য, পদ্যে পদ্যে ছয়লাপ। কবিতা সম্পর্কে নতুন এবং বিতর্কমূলক ভাবনা চিন্তার প্রবন্ধও বিরল। সহাবস্থানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বহু লিটল ম্যাগাজিন আত্মহারা। বাজার চলতি কবির লেখা ছাপানোর জন্য তাঁরা লালায়িত। এতে নাকি পত্রিকার ওয়েট বৃদ্ধি হয়। ফলে, প্রতি পক্ষে, প্রতি মাসে কবিতার কাগজ প্রকাশ করেও কবিতার আন্তরিক এবং অনুসন্ধানী পাঠক তৈরি হয় না।
এস্টাব্লিশমেন্টের লোকদের সামনে রেখে হয়তো পুরস্কার বিতরণ ও বইপত্র বিক্রির উৎসব পালিত হয়, কিন্তু এরপর সবাই নীরব। তথাকথিত ভালো লাল্টুস কবিতার দিন শেষ হয়ে গেছে, জ্ঞানমূলক দার্শনিকতাসর্বস্ব কবিতা আজ অচল, অচল সেই প্রাচীন ছন্দমালা ও শ্লোগান সর্বস্ব পংক্তি, তবু কাতারে কাতারে চলেছে এরই মর্দন। লেখার আইডেন্টিফিকেশনের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।
সময়, মিডিয়ার সাম্রাজ্যবাদে আক্রান্ত। ঘর-সংসার, বেচা-কেনা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, সাহিত্য-সংস্কৃতি সব মিডিয়ার ডোমিনেশনে। আমাদের জীবনের উচিত-অনুচিতও মিডিয়া স্থির করে দেয়। উন্মাদ ইনটিউইশনে আক্রান্ত হয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি, কল্পনা করি, পদ্যসিক্ত হই। মিডিয়ার অনুশাসন মেধা ও চেতনাকে হ্যান্ডিক্যাপড করে। ইনটিউইশন ধাবিত মানুষের চেতনায় বিভ্রম ঘটে বারবার। এই বিভ্রম ও বিহ্বলতা নতুন কবিতা গ্রহণে অন্তরায়। অথচ, ইনটিউইশনকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে অপর চেতনার ভাষায় নির্মিত কবিতা হয়ে ওঠে নতুন কবিতা। পদ্য স্বতোৎসারিত। স্বজ্ঞামূলক আবেগ তার উৎসবীজ। সেখানে নির্মাণ বিনির্মাণের শৈলিচেতনা অবান্তর। উৎস থেকে উঠে বিভিন্ন অভিঘাতে সম্প্রসারিত না হয়ে উৎস মুখের বাহুল্যেই ফিরে আসে। সেখানে কবি যেন অভিনয় কুশল, নাটুকে স্বভাবকবি। আর মিডিয়ার কাজ যেহেতু নিপাট মনোরঞ্জন, সেহেতু পদ্যকেই তার খাতির, পৃষ্ঠপোষকতা। সেক্ষেত্রে দু'চারখানা কবিতা কখনো পিছলে বেরিয়ে যায়। সুদীর্ঘকাল ধরে চর্চিত দোদুল্লানির পরিবর্তন করতে গেলে পদ্যকার বাঁচেন না, বিপরীত হলে মিডিয়াও তাকে দুধের বাটি এগিয়ে দেবে না। কতগুলো নাটুকে আবেগ-বিহ্বল বাক্যে ওপর থেকে লিরিক ও ছন্দ চড়িয়ে দেওয়াটাই পদ্যকারের প্রধান স্বভাব কৌশল। তার কবিতা সেই অবস্থায় গল্পধর্মী, বিবৃতিময়, স্পষ্টভাবে অর্থপ্রবণ। প্রতি পংক্তিতে চিরন্তন দার্শনিকতা ন্যায়নীতি, পলকা প্রেম আর মানবিক উদারতার বন্যা। কবিতা মানুষেরাই পড়ে, গাধারা গরুরা কবিতা পড়ে না--- এই চিরন্তন জেনেও পদ্যকারেরা মাঝেমধ্যেই বলেন, মানুষের জন্য মানুষের ভাষায় কবিতা লেখা উচিত। পদ্যের আগ্রাসনে বাংলা কবিতার জগৎ আজ মুগ্ধতায় মগ্নকৃত। এমনকি বিভ্রান্ত। পদ্য পড়তে পড়তে লিখতে লিখতে শুনতে শুনতে নতুন নির্মাণের কবিতা আজ দুর্বোধ্য অভিধায় কলঙ্কিত। কারো বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ একবার প্রচারিত হলে, তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিভ্রান্ত পাঠকেরা তাঁকে বা তাঁদের এড়িয়ে চলতে থাকেন। মিডিয়া ঠিক ক'রে দেয়, কারা কবি, কারা কবি নয়। বহু পাঠকও সেইমতো কবিতার পাঠ নেন। বুঝলেও নেন, না বুঝলেও নেন। ধীরে ধীরে তিনিও প্রতিষ্ঠানের ভাষায় কথা বলতে থাকেন। তাঁর চাহিদাও সেইভাবে তৈরি হয়। তিনি যেন প্রতিষ্ঠানের চলন্ত বিজ্ঞাপন। প্রতিষ্ঠান বলতে বিশেষ কোনো হাউস নয়। বিশেষ কোনো প্রকাশন সংস্থা নয়। বহু লিটল ম্যাগাজিনও প্রতিষ্ঠানের প্রতীক ও প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। সেখানে প্রথমে দেখা হয় কবিতার বিষয়বস্তুটি কী, তাতে কাহিনি আছে কিনা, মিলনমূলক সমাপ্তি আছে কিনা, চাঁদ বা সূর্যের বা পতাকার উত্তোলন আছে কিনা, আছে কিনা তথাকথিত আবৃত্তিযোগ্য মধুর ভঙ্গিমা ও নাটকীয় মূর্ছনা। এখানে মারক্সিস্ট এবং নন-মারক্সিস্টদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়েই প্রাতিষ্ঠানিকতাকে ধরে রাখতে চায় সাহিত্যে।
এটা কোনো বিপ্লবাত্মক কথা নয় যে আমরা পোস্টমডার্ন কালখণ্ডে আছি। ইতিহাসের নিয়মে পোস্টমডার্নিটি এসেছে। এটা কোনো বাদ বা ইজম নয়, কোনো শিল্পের আন্দোলনও নয়। পরিবর্তিত সময়ের বিশেষ কিছু চিহ্নমাত্র। কবিতার ক্ষেত্রে পোস্টমডার্নিটি নতুন কবিতাকে চিহ্নিত করে, যেহেতু নতুন কবিতায় ধারামুক্তির ওপর সার্বিক আলো ফেলা হয়েছে। পোস্টমডার্ন কালখণ্ডের কবিতাই অপরত্বের চিহ্নবাহী নতুন কবিতা, যা শৃঙ্খলাহীন। কবিতার আধুনিক বদ্ধমূল প্রকরণ থেকে মুক্ত সম্প্রসারিত চেতনার কবিতা। ভাবনা কেন্দ্রীয় বৃত্তবিন্দু থেকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে বহুমুখি রেখায়। কবি অবচেতনার স্তর থেকে বেরিয়ে পড়েন অপর চেতন বাস্তবে। পোস্টমডার্ন কালখণ্ডের কবিতা বিবৃতিময়তাকে অপর কবিতায় রূপান্তর ঘটায়, গল্পহীনভাবে প্রকাশিত হয়, ইজমকে ঠেকিয়ে রাখে। কবিতায় চেতনা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে উপযোগী নতুন ধ্বনিশব্দ, কল্পশব্দ, জোড়শব্দ প্রয়োজন মতো নতুন নামধাতুর নির্মাণ চলে। বর্জন করে এস্টাব্লিশমেন্টিয় গিমিক, পোস্টমডার্ন কালখণ্ডের কবিতা, নতুন কবিতা। কল্পনার বিনির্মিত আলো ভাষার তুমুল বদল ঘটাচ্ছে। পোস্টমডার্নিটির কথা বলেও কেউ যখন দর্শনাক্রান্ত মিঠিমিঠি পদ্যময় প্রতিবেদন লেখেন, তখন মনে হয়, পোস্টমডার্নিটি ডাইলিউট হয়ে গেল। পোস্টমডার্নিটিকে যখন ইজমের ফর্মুলায় ফেলা হয়, তখন তো আবার নতুন ক্যানন গড়ে উঠবেই। শুধু অভিজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞতার সম্ভাবনাতেও আলো ফেলছে পোস্টমডার্নিটি, যখন ক্যানন বিচ্যুত হয়। কারণ সে মুক্ত। বিষয়াবদ্ধ না হয়ে, বেরিয়ে পড়ার কথা বলছে অসীমের দিকে। সেই কারণে কবিতার ভাষায় নতুনভাবে এসেছে ক্যাওস, বিগঠন, ডি-মিথাইজড বিন্যাস, কেন্দ্রিয় চেতনার বিকেন্দ্রিকরণ। সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকতায় ব্যবহৃত অফিসিয়াল এবং অর্থোডক্স ভাষা থেকে মুক্ত হচ্ছে বাংলা কবিতা বিশ শতকের শেষ দিক থেকেই। নতুন কবিতার ভাষাই পোস্টমডার্ন কালখণ্ডের ভাষা, অটোমেটিক রাইটিং ও আধ্যাত্মিক হ্যাং থেকে বেরোনো। ফর্মুলাহীন। ইনোভেটিভ। ভাষায় অবিরাম স্পার্ক। ধ্বনির কবিতায়ন। বাংলা কবিতার ভাষা বিকশিত হয়েছে নতুন কবিতায়।
নতুন কবিতা সতত সৃজনশীল নির্মাণ প্রক্রিয়া যার অণুকণারা কেন্দ্র থেকে উৎসারিত হয়ে সম্প্রসারিত হতে থাকে বিভিন্ন ভাবনায়। আপাতভাবে মনে হতে পারে খাপছাড়া, শৃঙ্খলাহীন অদ্ভুত শব্দাস্ত্র ক্ষেপণ। প্রচল ভাষাবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন অন্য জগতের বিভাসা। অন্যত্রের ভাবনায় জারিত নতুন কবি দ্বিতীয় জীবন রচনা করেন প্রথম জীবনের রীতিবোধ, পাপপুণ্যতা, ক্লেদরতি ও দৈবিকের মিথ ঝেড়ে ফেলে। বিষয়কে পরিস্ফুট ব্যাখ্যার জন্য প্রবন্ধ মাধ্যম আছে, নীতিবোধমালার জন্য বাণীশিল্প, কবিতা এসবের আধার হতে পারে না। নতুন কবির কল্পনা সম্প্রসারণের পর্যায়গুলোতে কথ্য ও আভিধানিক শব্দের বিশিষ্টতা কবির কাছে যথেষ্ট নাও মনে হতে পারে। তাঁর বোধ অনুযায়ী বহু শব্দবিন্যাস চলতি ভাষায় সৃষ্ট হয়নি। ঝুঁকি নিয়ে আনন্দ পান একজন নতুন ভাষার কবি। তাঁর কাল্পনিক অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ অনুসারে এবং সংবেদনশীল মাত্রার সমন্বিত শব্দগুচ্ছে প্রয়োজনে কম্বিনেশনের বদল ঘটান। কখনো প্রচলিত শব্দে বাড়তি গুণারোপ দরকার পড়ে ধ্বনির সংযোজনে। কবির বোধব্যাপ্তি অর্থের মানদণ্ড তোয়াক্কা করে না।
বহুদিন হলো বাংলা কবিতা প্রতিকবিতার এবং নতুন কবিতার আবহে প্রবেশ করেছে। অটোমেটিক রাইটিংও চলছে প্রচুর। তবে অটোমেটিক রাইটিং থেকে প্রতিকবিতা ও নতুন কবিতা অন্তর্চেতনায় ও নির্মাণ প্রকৃতিতে অনেক আলাদা। বদলে গেছে ভাষার আদল, কবিতা এখন বহুমাত্রিক। কবিরা নিংড়ে নিচ্ছেন সমাজের নির্যাস, এমনকি নিজেকে। তথাকথিত ঋষিভাবুকতা ও প্রফেসরিজমের মুক্তি ঘটছে কাব্যধারায় এবং কবিব্যক্তিত্বে। এখন প্রতিকবিতার জন্য পাঠক তৈরি, নতুন কবিতার জন্য নতুন পাঠকও দেখা যাচ্ছে সর্বত্র। নতুন কবিতা শুধুমাত্র বোঝার ব্যাপার নয় বলে, এর জন্য অভিধানের দরকার পড়ে না। সাময়িকভাবে দূরের কোনো গ্রহের ভাষা মনে হতে পারে নতুন কবিতার ভাষাকে। যদিও এর এস্থেটিক্সের অনেক জায়গা এখনো আনএক্সপ্লোর্ডও মনে হবে। নতুন কবিতায় একজন কবির ভাষা অন্য কবির ভাষা থেকে একেবারে আলাদা।
*এই লেখাটি লিখিত হয়েছিল ১৯৯৯ সালে এবং প্রকাশিত হয়েছিল কবিতা ক্যাম্পাস পত্রিকার ২০০০ সালের জানুয়ারি সংখ্যায়। সামান্য সংশোধন করা হলো।

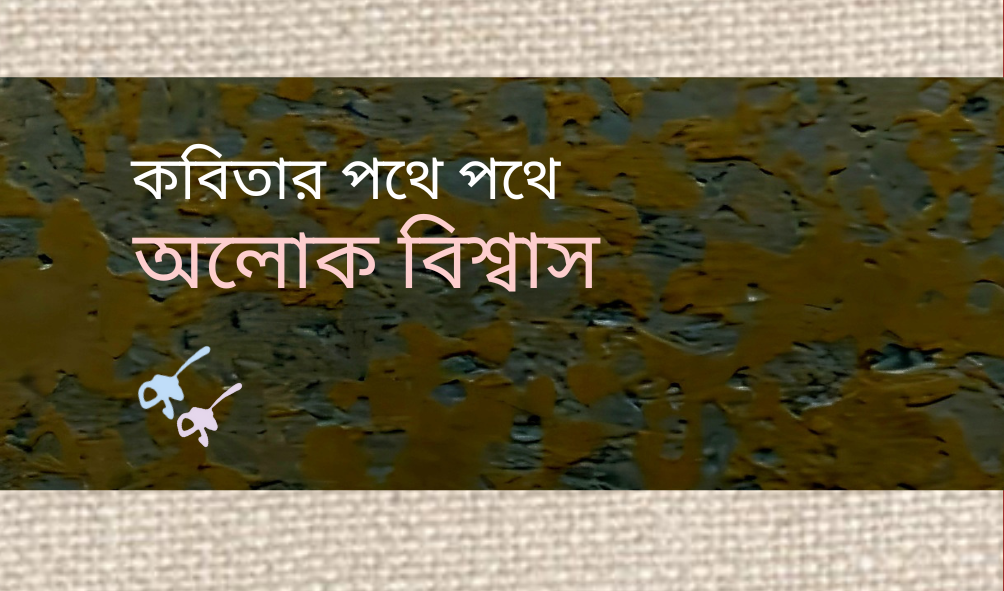
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন