জীবনানন্দের জনপ্রিয়তার আগে পর্যন্ত বাংলা কবিতা কমবেশি রবীন্দ্রনাথের মুখাপেক্ষী ছিল। আধুনিক মানুষ রবীন্দ্র প্রভাবিত লেখালেখি, প্রধানত কবিতা, পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন, মেনেও নিয়েছিলেন। চল্লিশের পর সেই জায়গা আস্তে ধীরে নিতে শুরু করেন জীবনানন্দ। জীবনানন্দ যে সময়ে লেখালেখি করেছেন তখন তারই সমসাময়িক অত্যন্ত শক্তিশালী একদল তরুণ পাশাপাশি লিখছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঁদের মধ্যে জনপ্রিয়তম হয়ে উঠলেন জীবনানন্দ, কারণ অন্যান্যদের কবিতার চেয়ে জীবনানন্দের কবিতার নকল করা তুলনামূলকভাবে সহজ। অপটু অশিক্ষিত হাতেও তা হতে থাকল। বাড়তে লাগল বাংলা কবিতার সংখ্যা, অবশ্যই চালুধারার এবং গতানুগতিক। এবং পাঠকও মিডিয়ার প্রচারে অভ্যস্থ হয়ে উঠলেন এইসব কবিতা পড়তে।
(১)
এই ধরণের কবিতা পড়তে পড়তে একসময় পাঠকেরও হয়ত মনে হতে পারে যে তাঁরাও কবিতা বুঝতে পারেন এবং মানেও করতে পারেন কবিতার। এই চিন্তাধারায় অভ্যস্থ পাঠক প্রথম ধাক্কা খেয়েছিলেন ষাটের দশকে, বিভিন্ন কবিতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে। তা যতই স্বল্পস্থায়ী হোক না কেন। কিন্তু আটের দশকে এসে ঐ একই পাঠকের কাছে বহু তরুণ কবির কবিতাই অচেনা মনে হতে লাগলো। একঝাঁক তরুণ কবি অন্যরকমের কবিতার চর্চা শুরু করলেন। যা রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ থেকে একেবারেই পৃথক। এবং এই অমিল কবিতার ফর্ম বা বহিরঙ্গে নয়, তা হল কবিতার মেজাজে বা অন্তর্জগতে। চালু কবিতায় অভ্যস্থ কবিকূল এবং পাঠক যথারীতি, সাময়িক হলেও, আবারো দুর্বোধ্যতার দোহাই দিতে থাকলেন। তারা ভুলেই গেলেন যে দুর্বোধ্যতাও আপেক্ষিক। যে কবিতা তাঁরা বুঝতে চেয়েও মানে করে উঠতে পারছেন না, সেই একই কবিতা অন্য আর এক আধজন পাঠকের অনুভবে বেজে উঠছে। কবিতার অনুভূতি তাঁকে কোনও এক অন্যমাত্রার জগতে পৌঁছাতে সাহায্য করছে, বাজিয়ে দিচ্ছে মনের ভিতর এক বিশেষ সুর। ফলে এই যে নতুন বা অন্যমাত্রার কবিতা লেখা হচ্ছিল, তা প্রথমাবস্থা থেকেই একেবারে পাঠকহীন ছিল না।
নতুন কবিতা লেখার এই যে প্রবণতা তা বিভিন্ন কবির লেখায় প্রতিফলিত হল। বা অন্তত সেই চেষ্টাটা দেখা যেতে লাগলো। নতুন কবিতা লেখার মাধ্যমরূপে কবিতায় তাঁরা পাল্টে ফেললেন শব্দ বা ভাষা ব্যবহার। এই রকম লেখালেখির যখন আট-দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তখন সর্বপ্রথম কবি ও প্রাবন্ধিক বারীন ঘোষাল এরকম লেখালেখির/কবিতার সমর্থনে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। এবং বাংলা কবিতায় তিনি অতিচেতনা-র কথা বলে এই ধরণের নতুন ও অন্যমাত্রার কবিতা ও তার লক্ষণগুলোকে চিহ্নিত করতে থাকেন।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে নতুন কি? কি ভাবেই বা কবিতায় নতুনের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে। আমাদের চেতনা সাহায্য করে নতুন ও পুরানোকে চিহ্নিত করতে। বেদে বলা আছে: নতুন হল তাই যা ছিল অন্য কোন কিছু থাকারও আগে। সুতরাং যা আমাদের চেতনায় আগে ছিল তা নতুন কিছু নয়। আমাদের অভিজ্ঞতার যে পরিসর, তার পেরিফেরি বা পরিধির বাইরে আছে কাল্পনিক অভিজ্ঞতার জগৎ যা অতিচেতনার মূল কথা। অতিচেতনা ভেঙে দিতে থাকে এই সীমা, ছড়িয়ে পড়তে দেয় চেতনাকে। বারীন ঘোষাল বলেন: "ঐ যা ছিল সীমানার বাইরে, যার অস্তিত্ব টের পাচ্ছি অসাধারণ অবাক প্রতিফলনে তাকে extra consciousness বলা চলে।.... সীমানা ভাঙ্গার ফলে অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে ভাবনা ও ধারণাগুলো, যা আছে অথচ ছিল অনলব্ধ তার হঠাৎ ছোঁয়া দেয় ভীষণ অবকাশ যা অতিচেতনার পরিসর। একে extra বলাই ঠিক। অস্তিত্ব বোঝা যায় বর্ণনা করা যায় না।" এবং নতুন কবিতা লিখতে এবং নতুনের কাছে পৌঁছাবার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন-"যা আছে তা বাদ দিয়ে নতুন নিয়ম বা সিস্টেম গড়ে তোলায় এখন আনন্দ"। এই যে যা আছে তাকে নেগেট বা বাতিল করতে করতে নতুনের কাছে পৌঁছানো, নতুন বাস্তবতা ও বস্তুগুণ আবিষ্কার করা। যা আছে চালু এবং গতানুগতিক কবিতার পরিমণ্ডলে সেইসব একে একে বাতিল করতে করতে পড়ে থাকে যে অণু সম্ভাবনাটুকু, তারই বিস্ফারে লুকিয়ে আছে নতুন কবিতার বীজ। এই যে নতুনের সম্ভাবনা তা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আনকোরা হলেও পূর্বে এ কথা জ্ঞাত ছিল অনেকেরই। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি তার "Freedom from the known" এবং Explo- ration into insight এবং আরো অন্যান্য কয়েকটি বইয়ে নতুনের কাছে পৌঁছানোর এই রাস্তার কথা বিশদভাবে বলেছেন। নেগেশনের মাধ্যমে অনালকে পৌঁছে যাওয়া বা চেতনার সম্প্রসারিত এলাকার ধারণা কৃষ্ণমূর্তি ছাড়াও আরো পরে আমরা শুনি ফ্রিৎজোফ কাপরার লেখনীতেও।
শুধু তাই নয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্যোগ ও সময় সম্বন্ধে আধুনিকতা যে অটল বা অপরিবর্তনীয় ধারণা বা বিশ্বাস মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছিল, তা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। প্রধানত এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় বেশ কিছু পদার্থবিজ্ঞানী। সময় সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে চুরমার হতে দেখি ১৯৮০ সালে কৃষ্ণমূর্তি এবং পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড বোহমের দীর্ঘ কথোপকথনে, যা ধরা আছে তাঁদের "The ending of Time" বইটিতে। একথা বলা এ কারণে যে বাংলা নতুন কবিতা আজ বর্জন করেছে যাবতীয় ছুৎমার্গীতা। যে কোনও বিষয় বা রূপ আজ কবিতায় চলে আসছে অনায়াসে। যাকে উত্তর আধুনিক বা অধুনাস্তিকরা বলছেন-যুক্তির বাইরে বেরোনোর প্রবণতা, অপরিমেয় এলাকায় প্রবেশের উশখুশ, ফিক্সিটি এড়িয়ে যাওয়া বা পরিবর্তনের তল্লাশী।
(২)
কবিতার ক্ষেত্রে সম্ভবত পোষ্টমডার্নিজম বা অধুনান্তিকতা শব্দটি প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৪২ সালে ডাডলি ফিটস সম্পাদিত 'অ্যানথলজি অব কনটেম্পরারি ল্যাটিন আমেরিকান পোয়েট্রি'তে।
যদিও বলা হয় সাহিত্যে এই ধারণাটি প্রথম এনেছিলেন ইহাব হাসান। অধুনাস্তিক চিন্তা বা চেতনার এলাকা বিশাল তাই এটি কোনো গোষ্ঠী, চীৎকার, আন্দোলন, প্যারাডাইম ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ফলে নয় নয় করেও পৃথিবীতে অধুনাস্তিকতার বয়স সময়ের হিসেবে প্রায় ঘাট বছর, যদিও তা প্রসার লাভ করতে যথেষ্ট সময় নিয়েছে।
বাংলা কবিতার পাঠকের যখন যথেষ্ট পরিমাণে নতুন বা অন্যমাত্রার কবিতা চোখে পড়ছে, তখন অতিচেতনার পাশাপাশি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আমরা বাংলা কবিতা তথা সাহিত্যের বাতাবরণে অধুনাস্তিক লক্ষণগুলিকে চিহ্নিত হতে দেখি কবি ও প্রাবন্ধিক সমীর রায়চৌধুরীর ঐকান্তিক প্রয়াসের মাধ্যমে। এবং এই সঙ্গেই কবি ও প্রাবন্ধিক মলয় রায়চৌধুরীও অধুনাস্তিক ধারণা সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের পাঠককে যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। বর্তমানের ঐ সংগঠিত ও ব্যাপক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকতে দেখি কবি প্রভাত চৌধুরী, কবি ও প্রাবন্ধিক জহর সেনমজুমদার এবং আরো কয়েক জনকে।
অধুনাস্তিকতার আলোচনায় যে নামগুলো বারবার ঘুরেফিরে আসে তাঁরা হলেন জঁ ফ্রসোঁয়া লিওতার, জাক দেরিদা, মিশেল ফুকো, অ্যালসডায়ার ম্যাকইনটায়ার, রলাঁ বার্থ, রিচার্ড বোরটি এবং ইহাব হাসান। বাংলা সাহিত্যে যাঁরা অধুনাস্তিকতার ধারণা দিতে চেয়েছেন, তাঁরা অধুনান্তিক আলোচনায় পরিহার করার চেষ্টা করেন পোষ্টমর্ডান ধারণার ইউরো-সেন্ট্রিজমকে। বহুক্ষেত্রেই তাঁরা ভারতবর্ষ তথা বাংলার জল, মাটি, আবহাওয়া ও বিভিন্ন প্রেক্ষিতকে অধুনান্তিকতার বিচার্য বিষয়রূপে গণ্য করেন। অধুনান্তিক ধারণায় যে অভেদের সন্ধানে যাত্রা তা একে একে চিহ্নিত করেছে বহুকিছুকে। বাংলা কবিতা লিখতে এসে যাঁরা অন্যধরণের কবিতা লেখার কথা ভেবেছেন, তাঁদের গতানুগতিক ও চালু কবিতার বিপরীতমুখী এই যাত্রায় পায়ের তলায় মাটি জুগিয়েছে অতিচেতনা এবং কবিতায় বিপুলভাবে অধুনান্তিক লক্ষণগুলি চিহ্নিত করার মাধ্যমে।
বাংলা চালু কবিতায় যে যুক্তির অবতারণা করার প্রথা ছিল তা আগের বিভিন্ন দশকের দু-একজনের কবিতায় আক্রান্ত হলেও, সংগঠিত ভাবে প্রথম আক্রমণের মুখে পড়ে আশির দশকে এসে, কেননা একঝাঁক তরুণ কবি দলবেঁধে বা বিচ্ছিন্নভাবে ঐ অন্যমাত্রার কবিতার চর্চা চালাচ্ছিলেন। এই সময়েই দেখা যায়, যা জড় বা অনড় বস্তু বলে চিহ্নিত তা কবিদের কাল্পনিক অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্খার যৌথ আহ্বানে প্রাণ পেয়েছে। এর ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ে এতদিনকার সযত্ন লালিত যুক্তির ঐক্য, কেননা যুক্তির ঐক্যকে অস্বীকার করাতেই রয়েছে এই কবিতা রহস্যের মূল চাবিকাঠি। দেখা যায় শব্দ ক্রমশ হারাতে থাকলো তার পূর্বনির্ধারিত মানে, রইল না চিহ্ন বা ধ্বনির নির্দিষ্ট ইশারা। সাহিত্যে প্রাধান্য পেতে শুরু করল প্লুরালিজমের ঝোঁক, দেখা গেল বহুবর্ণের ওপেন এন্ডেড পরিণতি। কবিতা লেখার জন্য কবিরা যে আলাদা ভাষাশৈলী তৈরি করত এতদিন তা ক্রমশ ভেঙে যেতে লাগলো এই সময়কার কবিতায়। কথ্যভাষা ও কবিতার ভাষা হয়ে গেল একাকার, কবিতা পেল এক উচ্চতর সাম্য।
উল্লেখযোগ্য এই যে এই সব প্রবণতা আদৌ সীমাবদ্ধ নয় শুধু সাহিত্য বা কবিতায়। শিল্পের সমস্ত শাখায় যেমন সিনেমা, চারুকলা, স্থাপত্য, নাটক ইত্যাদিতেও অধুনান্তিক লক্ষণ ফুটে উঠতে
দেখা গেল। যদিও আধুনিকতা বা আধুনিক কবিতা তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সমস্ত উপায়ে চেষ্টা চালাচ্ছে। এটাই তাঁদের নিয়তি। আসলে চেতনা ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশে রয়েছে অতিচেতনা বা অধুনাস্তিকতার বীজ। মানুষের সমস্ত ভ্যালুজ বা মূল্যবোধের ক্রমপরিবর্তনে পাওয়া যাচ্ছে এধরণের শর্তগুলো। স্যামুয়েল বেকেট তো প্রশ্নই তুলেছেন মূল্যবোধের বৈধতা নিয়ে। তিনি সমকালীন লেখক কবি ও শিল্পীর কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ও সঙ্গতির অসারতার কথা বলতে চেয়েছেন। প্রত্যাখ্যান করেছেন মূল্যবোধের পিছনে যে নান্দনিক সম্ভাবনা তার পুনরুজ্জীবনকে।
(৩)
একথা বলা হয়ে থাকে যে, সম্ভাবনা অনেক তার মধ্যে ঘটিত হয় যে কোনো একটিই এবং সেটাই বাস্তবে ঘটেছে বলে ধরা হয়, আর বাকীগুলি রয়ে যায় সম্ভাবনার মধ্যে। সম্ভাবনার এই বিমূর্ততা এই সময়ের কবি বা শিল্পীর কাছে অত্যন্ত জরুরী। ১৯৯৮ সালে জার্মানীর পরিচালক Tom Tykwer তাঁর "Run Lola Run" ফিল্মে এই থিয়রি প্রয়োগ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। এই ফিল্মে একই ঘটনার তিনরকম সম্ভাব্যতা দেখানো হয়েছে, যার যে কোনো একটা ঘটতে পারতো। পৃথিবীব্যাপী চিন্তার এই সাজুয্য আমাদের এগিয়ে ভাবতে সাহায্য করে। ছোটবেলা থেকে আমরা ক্রমশ বড় হয়ে উঠি চিন্তা সংগঠিত করতে করতে। সেই চিন্তা যা যোগান দিয়েছে পুরানো বিদ্যালয়, অথোরিটি, পরিবেশ, গুরু, ধর্মইত্যাদি। আমরা দেখতে শিখি উপরোক্ত বিভিন্ন সংস্থা ও পরিবেশ থেকে। ফলে সেই দেখা হয় অন্যের দ্বারা বা অতীত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কয়েকটি নির্দিষ্ট র্যাশনাল ভিত্তিভূমি দেওয়া হয় এবং তাই হয়ে ওঠে পরিমাপের কোষ্টিপাথর। সবার উপরে একটা নির্দিষ্ট মতবাদ চাপাতে চাওয়ার উদ্দেশ্য থেকে যায় এর পিছনে। তারাই বলে দিতে থাকে কোনটা ঠিক এবং কোনটা বেঠিক।
উপরোক্ত অবস্থান থেকে যখন বিচার করা শুরু করেন একজন পাঠক তখন তিনি সমসময়ে লেখা কবিতাকেও যাচাই করতে চান, মানে বুঝতে চান তাঁর পুরানো সেকেণ্ড হ্যান্ড স্কুলিং থেকে পাওয়া মূল্যবোধের মাধ্যমে। আর সেখানেই ঘটে বিপত্তি। তিনি মেলাতে পারেন না তাঁর পেয়ে যাওয়া পুরানো বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এই সময়ে লেখা কবিতাকে। সমকালীন এই কবিতাকে অধুনান্তিক বা অতিচেতনা-যে নামেই ডাকা হোক না কেন তা তো কবিতাই। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উপরোক্ত দু'টি চেতনা যা বাংলা কবিতার বিভিন্ন লক্ষণকে চিহ্নিত করছে-তাদের মধ্যে মিল সুপ্রচুর।
বাংলা কবিতার পাঠক যখন সাররিয়ালিস্টিক কবিতার প্রভাবে কেন্দ্র অভিমুখে যাত্রা করা বাংলা কবিতায় অভ্যস্থ হয়ে উঠেছেন তখন এই সমসময়ে কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়া বা কেন্দ্রাতিগ কবিতার চর্চা শুরু করেন বেশ কয়েকজন তরুণ কবি একসঙ্গে এবং বিচ্ছিন্নভাবে। এবং অতিচেতনা ও অধুনান্তিক দু'টি চেতনা বা চিন্তাক্ষেত্রই চিহ্নিত করতে থাকে এই লক্ষণটিকে। পরে পরেই লক্ষ্য করা যায় বাংলা কবিতার যুক্তির বাইরে বেরোনোর প্রবণতা থেকে ক্রমে বিপন্ন হয়ে উঠছে

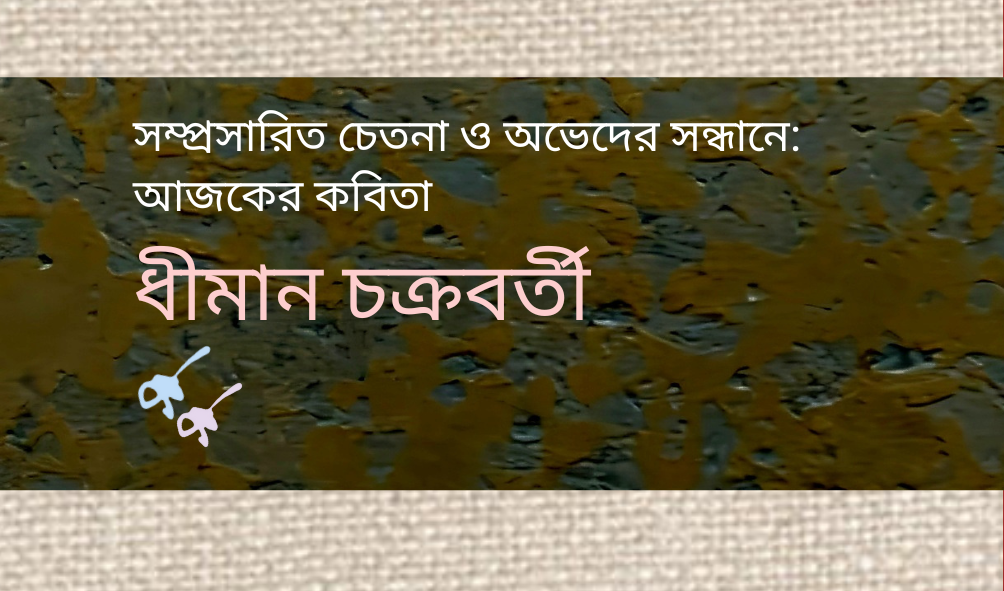
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন