প্রমিথিউস
প্রমিথিউস’কে নিয়ে চারটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।
প্রথমটিতে বলা হয়, প্রমিথিউস ঈশ্বরের গোপন রহস্য মানুষের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল। শাস্তিস্বরূপ তাকে ককেসাস-পাহাড়ের একটি পাথরে বেঁধে রাখা হয়। ঈশ্বর প্রতিদিন চিল পাঠাতেন তার যকৃৎ ছিঁড়ে খেতে। দিনের পর দিন ছিঁড়েখুঁড়ে খাবার পরেও প্রমিথিউসের যকৃৎ একই ছিল, যন্ত্রণা শেষ হত না; কারণ সেটি প্রতিদিন আবার বেড়ে উঠত।
দ্বিতীয়টিতে বলা হয়, চিলের তীক্ষ্ণ চঞ্চুর যকৃৎ ছিঁড়ে নেবার যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে প্রমিথিউস নিজেকে ক্রমাগত পাথরের ভেতর চেপে ধরতে থাকে। দিনের পর দিন সে নিজেকে পাথরের ভেতর চেপে ধরতে থাকে, যতদিন-না সে নিজে সেই পাথরে রূপান্তরিত হয়।
তৃতীয় কিংবদন্তি-মতে, হাজার-হাজার বছরের ব্যবধানে প্রমিথিউসের প্রতারণা ধীরে-ধীরে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়; ঈশ্বর ভুলে যান, চিলেরা ভুলে যায়, এমনকি প্রমিথিউস নিজেও ভুলে যায়।
চতুর্থ কিংবদন্তি অনুসারে, একসময় সবাই এই অর্থহীন বিষয়টি সম্পর্কে ক্লান্ত হতে শুরু করে। ঈশ্বর থেকে চিল- সবাই ক্লান্ত হয়। একদিন সেই ক্লান্তির পথ ধরেই ক্ষত বিলুপ্ত হয়েছিল।
পড়েছিল শুধু এক-তাল পাথরের মতো ব্যাখ্যাতীত দুর্বোধ্যতা।
কিংবদন্তি সে ব্যাখ্যাতীত’কে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল। সত্য খুঁজতে-খুঁজতে, তার ওপর থেকে বালি সরাতে-সরাতে কিংবদন্তি পৌঁছে গিয়েছিল ব্যাখাতীত কিছুর কাছে।
পাশের গ্রাম
আমার ঠাকুর’দা প্রায়ই বলতেন, ‘জীবন বড্ড ছোট। জীবনের দিকে তাকিয়ে মনে হয় আমি তার প্রায় কিছুই বুঝিনি। যেমন, ধরা যাক, একটা জোয়ান ছেলে পাশের গ্রামে যাচ্ছে। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে… আমি সে কথা না-হয় ধরলাম না; কিন্তু সে ভয় পাচ্ছে না। সে একবারও ভাবছে না যে গড়পড়তা মানুষের সুখী জীবনকাল বলতে আমরা যা বুঝি সেটা, এমনকি পাশের গ্রামে যেতে যতটা সময় লাগে, তার বহু আগেই শেষ হয়ে যেতে পারে।’
পাহাড়ে, ভ্রমণে
‘আমি জানি না,’ কেউ শোনে না; তবু আমি কেঁদে উঠি। ‘আমি জানি না... কেউ না এলে না-আসবে। আমি কারও কোনও ক্ষতি করিনি, কেউ আমার কোনও ক্ষতি করেনি। কিন্তু কেউ আমাকে সাহায্যও করবে না। একদল ‘কেউ-না’। তবু, এটাও একমাত্র সত্য নয়। একজনও আমার কাঁধে হাত রাখবে না জানি; কিন্তু তার বদলে একদল ‘কেউ-না’তো রইল। আমি ওই একদল ‘কেউ-না’র সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে যেতে চাই এখন। পাহাড় ছাড়া আর কোথায়ই বা যাবার আছে! সেখানে একদল ‘কেউ-না’ একে অপরের সঙ্গে খুনসুটি করবে, তাদের তুলে ধরা হাতগুলি সংযুক্ত হয়ে থাকবে। অসংখ্য পা খুব কাছাকাছি হেঁটে চলবে! সেই ‘কেউ-না’র দল চমৎকার ধোপদুরস্ত পোশাক পরে রয়েছে। আমরা আনন্দ করতে-করতে হাঁটছি; আমাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে হাওয়া। বাতাসও আজ আমাদের আনন্দসঙ্গী। পাহাড়ে আমাদের অনন্ত মুক্তি। কিন্তু আশ্চর্যের, আমাদের এই ‘কেউ-না’র দল গানে-গানে ফেটে পড়ছি না।
ম্যানর গেটে সেই টোকা
গ্রীষ্মের তপ্ত দিন; বোন’কে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফেরার সময়ে আমরা বিশাল একটা বাড়ির গেট পেরিয়ে চলেছিলাম। হঠাৎ আমার বোন সেই বিশাল বাড়ির বিরাট গেটে ধাক্কা দিয়েছিল, হয়তো দুষ্টুমি করে বা নিছক কৌতুহলের বশে। অথবা, সে হয়তো দরজায় ধাক্কা মেরে ভয় দেখাতেও চাইতে পারে; সঠিক কারণটা আমার পক্ষে এতদিন পর বলা অসম্ভব। একশো-পা হেঁটে গেলে রাস্তাটা বাম দিকে বেঁকে যাবে, সেখান থেকে গ্রামের শুরু। আমরা গ্রামটিকে ভালভাবে চিনতাম না; কিন্তু গ্রামের প্রথম বাড়ির সামনে আসতে না-আসতেই মানুষজন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছিল। তাদের কেউ-কেউ আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিল, কেউ-কেউ সতর্ক করছিল। বোঝা যাচ্ছিল তারা নিজেরাই ভয়ার্ত, ভয়ের চোটেই তারা গদগদ ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ছে। কারণটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, তারা ম্যানরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। সেই ম্যানর, যার গেটে আমার বোন ধাক্কা দিয়েছিল।
ম্যানরের মালিক আমাদের বিরুদ্ধে এরজন্য ব্যবস্থা নেবেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সালিশি শুরু হবে। আমি মাথা ঠান্ডা রাখতে চেষ্টা করছিলাম, বোন ভয় পেয়েছিল; তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলাম। হয়তো সে ইচ্ছা করে দরজায় ধাক্কা মারেনি, আর দরজায় ধাক্কা মারার জন্য পৃথিবীর কোথাও কারও বিরুদ্ধে আইন-আদালত করা যায় না। আমাদের সামনে বেশ কিছু লোকজন; আমি তাদের এই কথাটা বোঝাতে চাইছিলাম। তারা আমাদের কথা শুনছিল; কিন্তু, কোনও মন্তব্য করছিল না। পরে তাদের মধ্যে থেকেই কেউ-কেউ বলেছিল, শুধু আমার বোনকেই নয়, তার দাদা হিসাবে আমাকেও বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। আমি হেসে ফেলেছিলাম। সবাই মিলে ম্যানরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, ঠিক যেমনভাবে মানুষ ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে; ভাবে এবার আগুন বেরিয়ে আসবে। ঘোড়ার চড়ে সৈন্যরা খোলা গেট দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে ম্যানরের মধ্যে, ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে চারদিক। শুধু তাদের হাতে ধরে থাকা বর্শা-ফলার মাথাগুলো ঝকঝক করছে। ম্যানরের ভেতর ঢুকতে না-ঢুকতেই তারা আবার তাদের ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। তারা আমাদের খুঁজতে আসছে, বোনকে বলেছিলাম সেখান থেকে চলে যেতে। আমি সমস্ত বিষয়টা মিটমাট করে নেব। বোন আমাদের ছেড়ে যেতে চাইছিল না, অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে ছিলাম ম্যানরের সৈন্যরা ভদ্রলোক; তাদের সামনে আসতে হলে পোশাকটা অন্তত তার পালটে আসা উচিৎ। শেষমেশ সে কথা শুনেছিল, বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল। ঘোড়সওয়ার’রা এসে পড়েছিল, ঘোড়া থেকে না-নেমেই বোনের খোঁজ করেছিল। বলেছিলাম, সে এখন এখানে নেই, পরে আসবে। তাদের নিস্পৃহ ভঙ্গি বলে দিচ্ছিল বোনের ব্যাপারে তাদের এখন আর তেমন উৎসাহ নেই, তারা যে আমাকে খুঁজে পেয়েছে এতেই তারা খুশি। দলের প্রধান একজন ছটফটে লোক, সে আবার একজন বিচারক। একটা লোক চুপ করে ছিল, সে বিচারকের সহযোগী। তার নাম অ্যসমান। আমাকে খামারবাড়িতে ঢুকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মাথা নাড়তে- নাড়তে, প্যান্ট’টাকে টেনে-হিঁচড়ে তুলে হাঁটতে শুরু করেছিলাম, কতগুলো চোখ আমাকে আপাদমস্তক মেপে নিচ্ছিল। তখনও আমার ঘোর কাটছে না, তখনও আমার বিশ্বাস একটা মাত্র শব্দ আমার মতো একজন শহুরে মানুষকে এসব গেঁয়ো মানুষদের খপ্পর থেকে মুক্তি দেবার পক্ষে যথেষ্ঠ। বিচারকের ঘরের চৌ’কাঠ অতিক্রম করে দেখলাম তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, বললেন, ‘এ-লোকটার জন্য সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছে।’
আর সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, এ-কথাটার মধ্যে দিয়ে তিনি আমার বর্তমান অবস্থার কথা বোঝালেন না, বরং আমার সঙ্গে কী ঘটতে চলেছে সে দিকে ইঙ্গিত করলেন। ঘরটা যেন জেলের কুঠুরি। মেঝেতে ভারী পাথর, অন্ধকার দেওয়াল। দেওয়ালে লোহার রিং ঝুলছে। ঘরে মধ্যিখানে একটা কাঠের পাটাতন, অনেকটা টেবিলের মতো।
জেলের বাতাস ছাড়া আর কি অন্য বাতাস আমার ভাগ্যে জুটবে কোনও দিন? এটাই এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন। আরেকটা প্রশ্ন’ও থাকতে পারে- আমার মুক্তির কি আর কোনও সম্ভাবনা আছে!
আমাদের আইন ব্যবস্থার সমস্যা
আমারা আমাদের আইন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতে পারি না; আমাদের যে গুটিকয় মহামান্য মানুষ শাসন করেন তাঁরাই মোটামুটি আইন’কে নিয়ন্ত্রণ করেন। আমরা ধরে নিই এসব প্রাচীন আইনগুলি যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে তৈরি ও প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু আইন না-জেনে তার দ্বারা শাসিত হবার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা রয়েছে।
আইনের বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করতে গেলে নানা ধরণের পরস্পরবিরোধী মতামত উঠে আসতে পারে; আবার আইন ব্যাখ্যা করবার অধিকারও সবার থাকে না। সেটা থাকে গুটিকয়েক মানুষের হাতে। আমি সেগুলি নিয়েও তেমন চিন্তিত নই। এসব সমস্যার খুব একটা বেশি গুরুত্ব নেই। কারণ, আইনগুলি বেশ প্রাচীন, তাদের ব্যাখ্যাও হচ্ছে শতকের পর শতক ধরে। সেসব ব্যাখ্যাও আইনের মর্যাদা পেয়ে গেছে এতদিনে। হয়তো সামান্য কিছু নতুন ব্যাখ্যার অবকাশ আছে; যদিও তার পরিসর বেশ কম।
আবার গণ্যমান্য মানুষেরা আইনের এসব ব্যাখ্যা ব্যক্তিস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে করেছেন তেমনটাও মনে করবার কোনও কারণ নেই। কারণ, প্রথম থেকেই আইন তাদের সাহায্য করবার জন্যই তৈরি হয়েছে। গণ্যমান্যরা আইনের ঊর্ধ্বে। এ- কারণেই আইনের ভার তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আইনগুলির মধ্যে জ্ঞানের ছোঁয়া রয়েছে। প্রাচীন এসব আইনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা জ্ঞানকে সন্দেহ করবার কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদের জন্য রয়েছে প্রবল কষ্ট, সে কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া বেশ কষ্টের।
এসব আইনের অস্তিত্ব টিঁকে রয়েছে অনেকটা অনুমানের উপর ভিত্তি করে। সংস্কার আর ঐতিহ্য আমাদের জানিয়ে দেয় যে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে; যুগ-যুগ ধরে এ-ধারণা আমরা বহন করে চলেছি। রহস্যময় গোপনীয়তা ছাড়া রাজাউজিরদের এসব আইন টিঁকে থাকতে পারে না।
আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ সমাজের উঁচুতলার মানুষদের কাজকর্মের ধারা বহুদিন আগে থেকেই অনুসরণ করে আসছি; আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের সম্পর্কে কী লিখে গেছেন সেগুলির সন্ধান পেয়েছি। আমরা ভেবেছি ইতিহাসের গতিপথের বেশ কিছু ইশারা পেয়েছি; কিন্তু যখন বিক্ষণতার সঙ্গে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেয়েছি দেখেছি সবকিছুই কেমন যেন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। আমাদের কাজ শেষ পর্যন্ত মেধাচর্চার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কারণ, যে সমস্ত আইনগুলিকে আমরা উন্মোচন করতে চেয়েছি, দেখেছি তাদের অস্তিত্বই নেই।
একটা ছোট্ট পার্টি আছে, যারা এমনটাই বিশ্বাস করে। তাদের মত, আইন বলে যদি কিছু থাকে তা হল, হুজুরেরা যা করেন সেটাই আইন।
আইনের সম্মুখে
আইনের দরজার সামনে একজন পাহারদার দাঁড়িয়ে থাকে।
একদিন এই পাহারাদারের কাছে গ্রামের এক ছাপোষা মানুষ এসেছিল। দরজা পেরিয়ে তার ভেতরে প্রবেশ করবার ইচ্ছা। কিন্তু বাধ সাধল পাহারাদার, সে বলল ভেতরে প্রবেশ করবার অনুমতি তার পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর নয়। মানুষটি নিতান্ত ছাপোষা মানুষ; সে এটা নিয়ে আকাশপাতাল অনেক ভাবল। তারপর জিজ্ঞেস করল, পরে কখনও তার পক্ষে অনুমতি পাওয়া সম্ভবপর কি না।
পাহারাদার ভেবেচিন্তে বললো, ‘সেটা হয়তো সম্ভবপর; কিন্তু এক্ষুণি কিছু বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।’
দরজাটা হাঁ-করে খোলা, পাহারাদার দরজার একদিকে সরে গিয়েছিল; গ্রাম থেকে আসা মানুষটি শরীরটাকে নুইয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরের দিকে তাকিয়ে ছিল। গ্রামের লোকটার এভাবে ভেতরের দিকে তাকানো দেখে পাহারদার বেশ মজা পেয়েছিল, বলেছিল, ‘তোমার যদি এতই কৌতুহল তা হলে তুমি আমার বারণ না-শুনে ভেতরে যেতে পারো। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো- আমি শক্তিশালী। তবে পাহারাদারদের মধ্যে আমি সব থেকে কম শক্তিশালী। একবার ঢুকলে দেখতে পাবে, হলের পর হল-ঘর। একের পর এক পাহারাদার দাঁড়িয়ে রয়েছে। সব পাহারাদার তার আগের পাহারাদারের থেকে বেশি শক্তিশালী। একজন এমন কড়া আর শক্তিশালী পাহারাদার আছে যার চোখের দিকে আমিও তাকাতে পারি না; ভয় পাই।’
এখানে যে এত সব সমস্যার পাহাড় জমে রয়েছে তা গ্রাম থেকে আসা লোকটার কল্পনাতেও ছিল না। সে ভেবেছিল ‘আইন’-এর দরজা সবার কাছে সব সময় খোলা। লোকটা পাহারাদারের দিকে একবার ভাল করে নজর দিল। লম্বা টিকালো নাক; পরনে তার একটা পশমের কোট। দস্যুদের মতো লম্বা, কালো দাড়ি নেমে গেছে চিবুক ছাড়িয়ে। লোকটা ভাবলো, বেশি তড়িঘড়ি না-করে অনুমতির জন্য অপেক্ষা করাই ভাল।
পাহারাদার তাকে একটা টুল দিয়ে দরজার পাশে বসে অপেক্ষা করবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।
দিনের পর দিন চলে যায়, মাসের পর মাস। দরজার এক পাশে বসে লোকটি বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে থাকে। মাঝে সে বহুবার ভেতরে ঢোকার জন্য কাকুতিমিনতি করেছে; তার বেয়াড়া কৌতুহল দিয়ে পাহারাদারকে বিরক্ত’ও করেছে কিছুটা। পাহারাদারও যে তাকে একদম এড়িয়ে যায় তা নয়; মাঝে মাঝেই তার পরিবার নিয়ে এটা-সেটা প্রশ্ন করে। লোকটি বোঝে প্রশ্নগুলির মধ্যে অন্তরের ছোঁয়া নেই, নাম-কা-ওয়াস্তে সে সব প্রশ্ন করে চলা। রাজরাজড়ারা আমাত্যদের অনেক সময় এভাবে প্রশ্ন করে থাকেন। কিন্তু একটা জিনিস তার নজর এড়াইনি; প্রত্যেকবার কথার শেষে পাহারাদার এটা জানাতে ভোলেনি যে তাকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।
গ্রাম থেকে এতদূরে এসে লোকটি পড়েছে মহা-বিপদে। আসতে গিয়েই তার বেশ কিছু টাকাপয়সা খরচ হয়ে গেছে। তার ওপর পাহারাদারকে ঘুষ দিতে গিয়ে দামি জিনিসপত্র সব বেচে দিতে হয়েছে। পাহারাদার লোকটা বেশ অদ্ভুত। সে হাত-পেতে ঘুষ নেয়; কিন্তু প্রত্যেকবার বলে, ‘আমি এগুলি নিচ্ছি বটে; কিন্তু আমার নেবার তেমন কোনও ইচ্ছা ছিল না। তুমি কষ্ট করে এনেছো, তুমি কোনও চেষ্টা বাদ রাখছো-না ভেতরে ঢোকার জন্য। এই চেষ্টাকে সম্মান করা উচিত…।’
এই কয়েক বছর লোকটি পাহারাদারের উপর প্রায় সব সময় নজর রেখেছে। ভেতরে যে অন্য পাহারাদারেরা আছে তাদের কথা সে বেমালুম ভুলে গেছে। এখন তার মনে হয়, এই একমাত্র পাহারাদারের কারণেই সে ভেতরে ঢুকতে পারছে না।
প্রথম-প্রথম সে তার কপালকে দুষতো, প্রকাশ্যে নিজেকেই দোষ দিত। এখন তার বয়স হয়েছে; সে নিজের মনে গজগজ করে। সে এখন ছেলেমানুষের মতো হয়ে গেছে। দিনের পর দিন পাহারাদারের সঙ্গে প্রায় লেপটে থাকার ফলে সে এখন পাহারাদারের গায়ের আর কোটের গন্ধ চিনে গেছে।পাহারাদারের মর্জি বদল করার জন্য খড়কুটো আঁকড়ে বেঁচে থাকা মানুষের মতো সে এখন প্রায় সবাইকে অনুরোধ করে।
তার দৃষ্টিক্ষমতা কমে আসছে। আজকাল সে বেশ ঝাপসা দেখছে সব কিছু। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, পৃথিবীটা কি সত্যিই অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে; না কি তার চোখ তার সঙ্গে প্রতারণা করতে শুরু করেছে।
তবু সেই আধো-অন্ধকারের মধ্যেও সে অনুভব করে, আইনের দরজার কাছ থেকে একটি আলোর স্রোত তার দিকে ধেয়ে আসছে।
তার দিন শেষ হয়ে আসছে। মৃত্যুর আগে এই দীর্ঘ বছরগুলির সব অভিজ্ঞতা তার মাথার একটা খোপে যেন ভীড় করে আসছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটা প্রশ্ন, হয়তো এটাই শেষ প্রশ্ন, তার করা হয়নি পাহারাদারকে।
অশক্ত শরীর নিয়ে তার আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই; সে হাত নেড়ে পাহারাদারকে ডেকে ছিল।
পাহারাদারকে বেশ নিচু হতে হয়েছিল; এমনিতেই তাদের মধ্যে উচ্চতার তফাৎ ছিল। এখন মানুষটার অক্ষমতার কারণে সেটা আরও বেড়েছে।
‘তুমি এখন কী জানতে চাও? তোমার তো কৌতুহল মেটেনি, ভেতরে-ভেতরে তো তুমি ছটফট করছো,’ পাহারাদার ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেছিল।
লোকটা ধুঁকতে-ধুঁকতে বলেছিল, ‘সবাইতো আইনের কাছে পৌঁছানোর জন্য মরিয়া চেষ্টা করে, হাপিত্যেশ করে। কিন্তু কী এমন ঘটল যে সবাই ঢুকতে পেলো আর আমাকে বছরের পর বছর শুধু অনুমতি পাবার জন্য অপেক্ষা করে যেতে হল?’
পাহারাদার বুঝেছিল লোকটির সময় ঘনিয়ে এসেছে; এর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জোরে না-বললে বেচারি কিছুই শুনতে আর বুঝতে পারবে না।
পাহারাদার লোকটির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, ‘শোনো, এখানে কোনওদিন কাউকে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর এ-দরজাটাও একমাত্র তোমার জন্যই বানানো হয়েছিল। এবার আমি দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি…।’
একদিন, ট্রামে
ট্রামের সব থেকে পিছনের সিঁড়িতে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং এই পৃথিবীতে, এ-শহরে অথবা আমার পরিবারে আমার অবস্থান ঠিক কী সে বিষয়ে পুরোপুরি উদাসীন ছিলাম। কোনও দিকেই আমার যাবার ছিল না। ট্রামের এই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ, কেনই বা আমি হাতল ধরে রয়েছি, কেন আমি ট্রামে চড়েছিলাম আর কেনই বা ট্রাম আমাকে নিয়ে চলেছে- সে বিষয়ে আমার কিছুই বলার ছিল না। শহরের পথচারী’রা একপাশে সরে গিয়ে ট্রামকে পথ করে দিচ্ছে, কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে দোকানের শোকেস’গুলির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এসব কোনও কিছু নিয়েই আমার কিছু বলার ছিল না। যদিও কেউ আমাকে কিছু বলতে বলেওনি।
ট্রাম একটা স্টপেজে এসে থেমেছিল; একটি মেয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে ট্রাম থেকে নামবে। মেয়েটি আমার কাছে এতটাই স্পষ্টভাবে ধরা দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমি যেন তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।
সে আজ কালো পোশাক পরেছে। তার স্কার্টের কুঁচি স্থির হয়ে ঝুলে রয়েছে। গায়ে এঁটে রয়েছে টাইট ব্লাউজ। ব্লাউজের গলার কাছে ঘন বুননের লেস্। তার বামহাত ট্রামের দেওয়ালের একদিকে ছড়ানো, ডানহাতে ধরা ছাতা দ্বিতীয় সিঁড়িতে।
মেয়েটির মুখ বাদামী রঙের, নাকের পাটা দু’দিকে সামান্য চাপা। কিন্তু নাকের উপরের অংশটা বেশ চওড়া, গোলাকার। তার মাথায় ঘন বাদামী চুল; কপালের ডানদিকে চুলের হালকা গোছা পাক খেয়ে নেমেছে। ছোট-ছোট দু’টি কান বেশ চাপা; কিন্তু কাছে গিয়ে দেখেছিলাম ডান-কানের ভেতর তরঙ্গের মতো অদ্ভুত সুন্দর ধাপ। সেগুলি কানের আরও গভীরে নেমে গেছে।
আর, ট্রামের সব থেকে পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে আমি আমি নিজেকেই প্রশ্ন করছিলাম; জানতে চাইছিলাম, এই নারী কেন নিজেকে দেখে নিজেই আশ্চর্য হয় না? কেন সে দুটি ঠোঁট বন্ধ করে চুপ করে রয়েছে?
কেন সে কোনও শব্দ করছে না...
প্রত্যাখ্যান
এক একদিন কোনও সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আমি সাহস করে বলি, ‘আমাদের দু’জনের মধ্যে একটু কথা হতে পারে কি?’
মেয়েটি কোনও উত্তর না-দিয়ে চলে যায়। সে যেন বলতে চায়, ‘তুমি কোনও নামজাদা ডিউক নও। রেড-ইন্ডিয়ানের মতো লম্বাচওড়া চেহারার আমেরিকান নও। আমার স্বপ্নের সে রেড-ইন্ডিয়ানের চামড়া পুষ্ট হয়েছে প্রেইরি তৃণভূমির হাওয়ায় আর তার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর জলে। বিশাল-বিশাল হ্রদ আর নদনদীতে তুমি অ্যডভেঞ্চার করোনি। আমার স্বপ্নের পুরুষের কোনও গুণ তোমার নেই। তা হলে আমার মতো একজন সুন্দরী মেয়েকে কেন তোমার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে বলছো?’
‘তুমি ভুলে যাচ্ছ, কোনও ময়ূরপঙ্খী নাও তোমার জন্য অপেক্ষা করে নেই। কোনও লিমুজিনে তোমাকে চাপিয়ে কেউ হুস করে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে না। যুবকের দল ধোপদুরস্ত পোশাকে তোমার পিছু নেয়নি। তোমার বুক বেশ ঢাকাঢুকি দেওয়া আছে অন্তর্বাসে, কিন্তু ঊরু আর নিতম্ব সে আড়াল পুষিয়ে দিয়েছে। তুমি কুঁচি দেওয়া একটা সিল্কের পোশাক পরে আছো; গত শরতকালেও আমরা এটা দেখে বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম। যাই হোক, এ-বিপদজনক পোশাকেও তুমি মাঝে-মাঝে হেসে ওঠো।’
‘হ্যাঁ, আমরা দু’জনেই ঠিক কথা বলছি। আমাদের কারও কথাকেই যুক্তি দিয়ে অগ্রাহ্য করা যাবে না, দু’জনেরই খুব তাড়াতাড়ি এটা বোঝা উচিত। তুমি কি মনে করো না, যে এই কারণেই আমাদের আলাদা-আলাদাভাবে বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত?’
গাছেরা
কারণ, আমাদের অস্তিত্ব বরফের মধ্যে গাছেদের গুঁড়ির মতো। দেখে মনে হবে, গুঁড়িগুলি আলতোভাবে শুয়ে রয়েছে, সামান্য একটু ধাক্কা দিলেই বরফের মধ্যে সেগুলি গড়াতে শুরু করবে। কিন্তু এমনটা হবে না। কারণ, সেগুলি মাটিতে প্রোথিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু, এও এক ধরণের বিভ্রম, চোখের ভুল।
কাফকা- কয়েকটি কথা
কাফকা এমন এক মহাজাগতিক বুব্যিট্রাপ যার থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। তিনি সেই স্রষ্টা যিনি কয়েকটি মাত্র লাইনের এক ফেবল-এর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন জীবনের মহা-সত্য’কে। কাফকার ‘মেটামরফসিস’ নিশ্চয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিগুলির মধ্যে অন্যতম; কিন্তু তাঁর এই ছোট ছোট গল্পগুলির দিকে আরও বেশি করে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কাফকা তাঁর A Little Fable নামে একটি গল্পে লিখছেন,
"Alas," said the mouse, "the world is growing smaller every day. At the beginning it was so big that I was afraid, I kept running and running, and I was glad when at last I saw walls far away to the right and left, but these walls have narrowed so quickly that I am in the last chamber already, and there in the corner stands the trap that I must run into." "You only need to change your direction," said the cat, and ate it up.
-প্রতিদিন একটি ইঁদুরের কাছে তার পৃথিবী ছোট হয়ে আসছিল, সে ছুটতে শুরু করেছিল এবং একদিন সে ডাইনে-বামে দেওয়াল দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু নিয়তির মতো তার কাছে প্রতি মুহূর্তে সংকীর্ণ হয়ে আসছিল দেওয়াল দুটির মধ্যে ফাঁক, সে এসে পৌঁছেছিল এমন এক প্রান্তে যেখান থেকে তার আর ফেরার উপায় নেই। সেখানে একটি ফাঁদ পাতা। অবশেষে বিড়ালটির কাছ থেকে সে শুনেছিল সেই চূড়ান্ত দর্শন, ‘বহু আগেই তোমার দিক পরিবর্তন করার দরকার ছিল।’
এরপর বিড়াল যে ইঁদুরটিকে খাবে সে নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু গল্পটির মধ্যে একমাত্রিক আধুনিকতার করুণ পরিনাম খোদিত করে রেখে দিয়েছেন কাফকা।
মিথ, মিথের পুনর্নিমাণ কাফকার প্রিয় নির্মাণ-কৌশল। বুর্জোয়া ও পোস্ট-ট্রুথের পৃথিবীর ছায়ায় হেঁটে যেতে যেতে কাফকা’কে আজ আরও বেশি করে আবিষ্কার করা যায়। কাফকার ন্যারেটিভের মধ্যে লুকিয়ে থাকা জাদু আমাদের বহু সুগার-কোটেড পিল গলে নিতে বাধ্য করে। এই পিলগুলির মধ্যে যদি একটা হয় মিথ’কে ভেঙেচুরে তার মুখোশ খুলে দেওয়া, তা হলে আরেকটি হল ঘাতক সিস্টেমের বাইরে থেকে সকৌতুকে তার দিকে তাকিয়ে থাকা ও তাকে প্রশ্ন করে চলা। অনেক সময়েই ‘গল্পের’ ভিতর থেকে ‘গল্পের’ উপাদানকে শুষে নিয়ে তাকে একপাশে সরিয়ে রেখেছিলেন কাফকা। ‘দ্য জাজমেন্ট’ ‘ইন দ্য পিনাল কলোনি’ থেকে শুরু করে ‘অ্য হাঙ্গার আর্টিস্ট’ – একের পর এক গল্পে কাফকা নির্মাণ করেছিলেন তাঁর অতি-বিখ্যাত কাফকায়েস্ক পৃথিবী।
কাফকার ন্যারেটিভের চরম নিদর্শনের মধ্যে অবশ্যই থাকবে ‘দ্য গ্রেট ওয়াল অফ চায়না’ গল্পটি। চিনের প্রাচীর নির্মিত হবার পিছনে যে কাহিনি মিথ রাজতন্ত্র ও ফিউডাল সিস্টেমের গূঢ় সংযোগ সেগুলিকে উন্মোচন করতে করতে এগিয়ে চলেছিলেন কাফকা। সত্যি সত্যি এমন কোনও ঘটনা ঘটেছিল কি না সে বিষয়টিই এক সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে আসে; এই গল্পটির এক জায়গায় আমরা পেয়ে যাচ্ছি,
‘এই যে মহা-প্রাচীর, সেটা কাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে তৈরি করা হয়েছিল?
উত্তরের দস্যুদের হাত থেকে নিস্তার পেতে।
এবার চিনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের দিকে নজর দেওয়া যাক। উত্তরের কোনও মানুষের সেখানে নাক গলানোর বা বিন্দুমাত্র সমস্যা তৈরি করার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। প্রাচীণ গ্রন্থে আমরা তাদের কথা পড়েছিলাম মাত্র; তাদের স্বভাব আর নিষ্ঠুরতার কথা ভাবতে ভাবতে আমরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতাম। শিল্পীদের নিখুঁত তুলিতে ফুটে উঠত তাদের ভয়ংকর মুখ, তাদের পশুর মতো দাঁত। সে দাঁতে একদিন যারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তাদের কথা মনে পড়ত আমাদের। বাড়ির ছোটরা যখন দুষ্টুমি করত আমরা তাদের এইসব ছবি দেখাতাম, ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে তারা আমাদের বুকে মুখ গুঁজে দিত। কিন্তু উত্তরের এই সব দস্যুদের সম্পর্কে আমরা এর থেকে বেশি কিছুই আর জানতাম না। আমরা তাদের কোনও দিন দেখিনি। এমনকি আমরা আমাদের গ্রামে বাস করলে তাদের মুখোমুখি হবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তারা ঘোড়ায় চেপে প্রান্তরের পর প্রান্তর পেরিয়ে এলেও আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ যোজন যোজন মাইল শূন্য প্রান্তর পেরিয়ে আমাদের কাছে তাদের পৌঁছে যাওয়া ছিল অসম্ভব।
তা হলে কেন আমরা আমাদের গ্রাম ছেড়ে, ভাই বোন মা-বাবাকে ছেড়ে আমাদের স্ত্রীদের ছেড়ে দূর শহরের দিকে চলে গেছিলাম? কেন?
শুধু মাত্র উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আদেশ পালন করব বলে’।
-ক্ষমতা কীভাবে দিনের পর দিন ফিয়ার-সাইকোসিস তৈরি করে তার নিজের স্বার্থে, কীভাবে সে বুনে দেয় ভয় ও ঘৃণার বীজ তার চমৎকার এক প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পটিতে। চিনের প্রাচীর হয়ে উঠছে রহস্যময় এক নির্মাণ, যার অন্য দিকে পড়ে রয়েছে হাজারো প্রশ্ন ও সম্ভাবনার জগত।
ফ্রানজ কাফকার গল্পে ‘টাইম-ট্রাভেলের’ কাজটি করে দেয় স্মৃতি ও নস্টালজিয়া। ‘মেটামফোসিস’-এও তাই ঘটেছিল, গ্রেগর সামসা অতিকায় পতঙ্গে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু তার স্মৃতি যুক্ত হয়েছিল অতীতে।
কাফকার গল্প পড়তে পড়তে আজ আরও একবার মনে হচ্ছে, শিল্পের কোনও দায় নেই নিছক ‘সুন্দর’ হয়ে ওঠার। সৃষ্টি, মানুষের জীবন, জীবনের মধ্যে মিশে থাকা ‘কন্ট্রাডিকশন’, অতি-গুপ্ত হিংসা ও দ্বেষ – শিল্প আসলে ধারণ করে থাকে এসবই। কাফকা আমাদের দেখাচ্ছেন, গ্রেগরের বাবা একটি মিউজিক স্ট্যান্ড নিয়ে এসে বসিয়ে দিচ্ছেন তার মেয়ের সামনে, গ্রেগরের বোন ভায়োলিন বাজিয়ে চলেছে তিনজন বোর্ডারের সামনে…এই দৃশ্যটির মধ্যে কোথাও নেই গ্রেগর সামসা। এবং সে নেই বলেই ভায়োলিন তিনজন বোর্ডার তার মা-বাবা – সব মিলিয়ে দৃশ্যটির মধ্যে তৈরি হচ্ছে নিষ্ঠুরতা, যে নিষ্ঠুরতা পতঙ্গ পরিণত হয়ে যাওয়া এক মানুষের অসহায়তার পাশে আরও বেশি করে ফুটে থাকে।
কিন্তু গ্রেগর সামসা কি অসহায় ছিল? তার স্বপ্নে ঘটে যাওয়া ও পতঙ্গ-জীবনকালে অভিজ্ঞতাগুলির বহু ফ্রয়েডিয়ান ব্যাখ্যা আছে। এবং কাফকার গল্পের পাঠকের অনন্ত স্বাধীনতা আছে প্রতিদিন প্রতিবার প্রতিটি শব্দের নতুন নতুন ইন্টারপ্রিটেশন করার।
কাফকার প্রোটাগনিস্ট গ্রেগর সামসা বিমূঢ় করে রেখে দেওয়া জীবন, তার জটিলতা ও পরস্পরবিরোধীতার চূড়ান্ত প্রকাশ; এক সময়ে এমনই মনে হত। সামসা হয়তো চেয়েছিল একটি পতঙ্গের জীবন যাপন করে এই বিমূঢ় করে রাখা জীবন-রহস্যের সন্ধান পেতে।
কিন্তু কোথাও কি আমার-আপনার কখনও মনে হয়নি গ্রেগর আসলে যা কিছু প্রথাগত যা কিছু মূলধারার অংশ তার বিপ্রতীপ এক অবস্থান, যে অবস্থান আসলে সে নিজেই নির্বাচন করে নিয়েছিল!
কাফকার জগতে লুকিয়ে রয়েছে সেই distortion যা শিল্প’কে সার্থক করে তোলে, যা আদপে দেখিয়ে দেয় ভয়ংকর প্যাটার্নকে।
কাফকা তাঁর ‘কাফকায়েস্ক’ পৃথিবী থেকে তাকিয়ে ছিলেন আমাদের পৃথিবীর দিকে, পবিত্র distortion-এ ভরা পৃথিবী থেকে দেখা আমাদের সে জীবন, হতে পার পোকামাকড়ের।

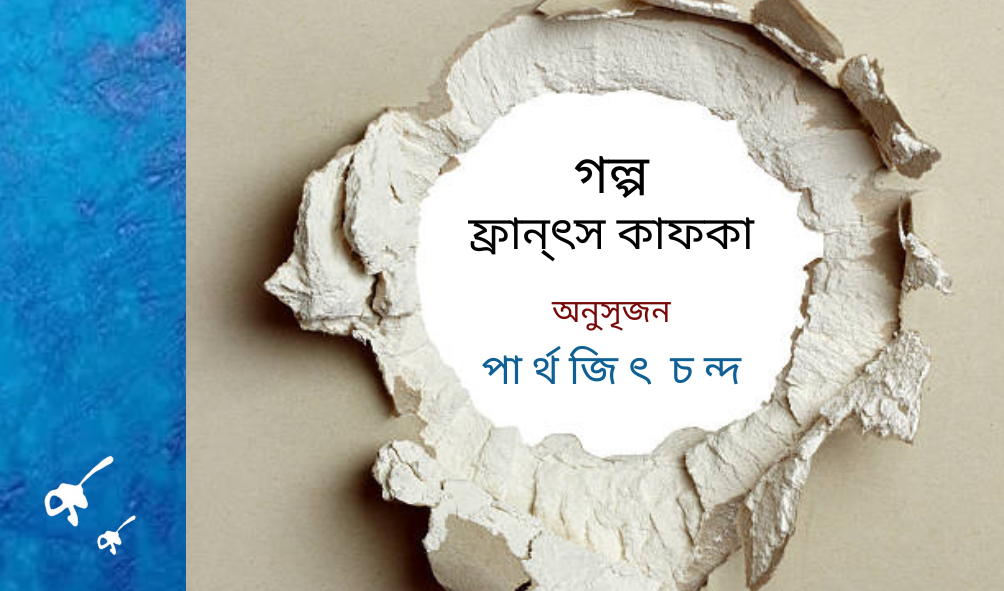
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন