শেষের দিকে উনি যখন বালিগঞ্জ প্লেসের 'পাঠ-ভবন' স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হন, তখন প্রায়ই আমাদের ৩৬ নম্বরে দুপুরের আহার এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম সেরে আবার স্কুলে ফিরে যেতেন। আগের থেকেই আমার বড়ো কাকীমা (মামণি)-কে বলে দিতেন, ফোনে অথবা সকালে স্কুল যাওয়ার পথে: "শান্তিদা আজ দুপুরে তোমার ওখানে খাব। একটা ভাত, একটা মাছ, একটা তরকারী, একটা ডাল ব্যস।" মামণির মামাতো ভগ্নীপতি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। আর ওই সম্পর্কের সুবাদেই আমরা ওঁর ডাকনাম বটুক মেসোমশাই বলেই ডাকতাম। ফলে এ-লেখায় মাঝেমধ্যে 'বটুক মেসোমশাই' এই সম্বোধনটি এসে যেতে পারে।
যাইহোক, উনি আসতেন, খেতেন, তারপর কাকার সঙ্গে পাশাপাশি খাটে শুয়ে নানা গল্পের মধ্যে একটা কথা প্রায়ই বলতেন: "প্রবোধদা, আমার কী ইচ্ছে জানেন, রবীন্দ্র সংগীত যেমন সংগীতের একটা ধারা, সেইরকম জ্যোতিরিন্দ্র সংগীতের একটা ধারা তৈরি হোক।"
আমি জ্যোতিরিন্দ্র অর্থাৎ বটুক মেসোমশাইয়ের কথা বলছি। বলছি, গণসংগীতের পুরোধা, 'নবজীবনের গান' 'মধুবংশীয় গলি'-র কবি ও সংগীতকার কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কথা। মামণির মামাতো বোন উর্মিলা মাসির স্বামী মহাপ্রতিভাধর, ছন্নছাড়া, খামখেয়ালি একজন মানুষের কথা বলছি।
বটুক মেসোমশাইয়ের শ্বশুরবাড়ি (অর্থাৎ মামণির মামার বাড়ি) ৬ নম্বর রিচি রোডে। সেখানে উনি যেতেন প্রায়ই অদ্ভুত অদ্ভুত পোশাকে। এ সব তাঁর যৌবনের কথা। মামণির মুখে শোনা। রিচি রোডের বাড়ির কোনো এক অনুষ্ঠানে উনি উপস্থিত হন সোনালি বুটিদার লাল পাগড়ি মাথায়, মাঝখানে নয় বুকের বাঁ-পাশে বোতামের পট্টি, গাঢ় বেগুনি রঙের পাঞ্জাবি, ধুতি মালকোচা দিয়ে, পায়ে বাদামি রঙের শুঁড় তোলা হয়তো বিদ্যাসাগরীয় চটি। ওঁর শ্বশুর বিনয়েন্দ্রপ্রসাদ বাগচী বলে উঠতেন: "আঃ, বটুককে নিয়ে আর পারা যায় না। কী এক অদ্ভুত পোশাকে এসেছে, লোকে বলবে কী, একদম পাগল।” জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর বিবাহের পর উর্মিলা মাসির কোলে মাথা রেখে প্রেমালাপে যদি কেউ যোগ দিত, বিশেষত শ্যালক-শ্যালিকা গোছের, উনি তো বেজায় খুশি।
আমাদের ৩৬ নম্বর বাড়িতে উর্মিলা মাসিসহ বটুক মেসোমশাই প্রায়ই আসতেন। পাগড়ি থাকত না বটে, তবে ওঁর পোশাকে তেমন কোনো হেরফের দেখিনি। যতদূর মনে পড়ে, গেরুয়া পাঞ্জাবি ঢোলা হাতা, বুকের বাঁ-পাশে যথারীতি বোতামের পট্টি, মালকোচা মারা ধুতি, পায়ে বিদ্যাসাগরীয় বা অন্যরকমের চটি। এসেই আমাদের বাড়ির একতলার পূর্বদিকের ঘর, বসবার ঘর, সেখানে ঢুকে যেতেন। ঘরে ছিল মস্ত একটা পিয়ানো, সেটি খুলে, রবীন্দ্রসংগীতের ফুল ফুটিয়ে যেতেন। কখনো চিত্রাঙ্গদা, কখনো শ্যামা, রবীন্দ্রনাথের যখন যে-গানটি গাইতে ভালো লাগত- একা তন্ময় হয়ে উনি গেয়ে চলেছেন। কে শুনছে, কে শুনছে না, এইসব চিন্তা উনি ওঁর ধর্তব্যের মধ্যেই রাখতেন না।
সংগীতের শুধুমাত্র একজন সাধারণ শ্রোতা হিসেবে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুর যে সম ওজনের, কথা যেমন সুরে ছড়িয়ে যাচ্ছে, সুরও তেমনি কথাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অল্পবয়স আমার, সেইবয়সে জ্যোতিরিন্দ্রের গান শোনার মহাসৌভাগ্য আমার হয়েছে বলেই রবীন্দ্রসংগীতের এই গোপন রহস্যটি আমি বুঝেছিলাম। সঠিক সুরকে বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথের গানকে উনি জীবন্ত করে তুলতেন। এ সেই তথাকথিত স্বরলিপি ভাঁজা অথবা ভাঙা প্যানপ্যানে রবীন্দ্রসংগীত নয়। এ এক নির্ভুল, দানদার জোরালো সুরসমৃদ্ধ কণ্ঠস্বর।
একবার মনে আছে, সন্ধেবেলার বা রাত্তিরেও হতে পারে একটি রেডিয়ো প্রোগ্রামে বটুক মেসোমশাইয় গাইছেন: "মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই।” সমস্ত বালিগঞ্জ প্লেস পাড়াটা ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। পাশের বাড়িতে আমাদের এক জ্যাঠামশাই থাকতেন, তিনি, বাবা ও কাকা বলতে লাগলেন, বটুক আজ প্রাণটা ভরিয়ে দিয়ে গেল।
এখন বুঝি, বহুগুণের অধিকারী হলেও, উনি প্রধানত একজন গানেরই মানুষ। গানই ওঁর জগৎ। ওঁকে সেভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে দেওয়া হয়নি। উনি সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস- এঁদের যে দিশারী ছিলেন, আজ বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারি। একটি রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানে টিকিট কেটে
দুই রবীন্দ্রসংগীতপ্রেমিক পলিদা ও সোমেশবাবু জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের গান শুনতে গিয়েছিলেন। শান্তিদেব ঘোষ অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক। সকলেই একাধিক গান গাইলেন। জ্যোতিরিন্দ্র গাইলেন একটি গান- 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।' পলিদারা ব্যর্থ মনোরথ। ব্যাপার কী, একটি গান মাত্র! পলিদা আমাকে বলেছিলেন, ঈষৎ বিষণ্ণতা মাখনো হাসি বটুকদার: "আমি তো রবীন্দ্রসংগীতের ওই একটি গানই জানি।"
মনে আছে, আমাদের বাড়িতে পিয়ানোতে যখন খোলা কণ্ঠে (open voice) উনি গাইতেন "সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্থান হামারা, হিন্দি হ্যায় হাম হিন্দি হ্যায় হাম" গানটি, তখন আমার মনে হত সমস্ত বাড়িটা দুলছে। মামণিকে যে উনি 'শান্তিদা' বলে সম্বোধন করতেন সেটি সম্ভবত শান্তিদেব
ঘোষকে 'শান্তিদা, শাস্তিদা' বলে উঠতি এমনকী প্রতিষ্ঠিতেরাও যে-রকম তোষামোদ করতেন সেইটি বাঁকা পথে ওঁর সংগীত জীবনে যথেষ্ট দুঃখের কারণ হয়েছিল।
উনি ছিলেন সুরসিক, সম্ভবত মামণিকে 'শান্তিদা' বলে ডেকে নিজের দুঃখকে নিয়ে মজা করতেন। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়েছে, আমাকে কবি কবি বলে চিৎকার করে ডাকছেন। কী যে বলি, খুবই সংকুচিত হয়ে ওঁর কাছে যেতাম, "কেমন আছ, লিখছ তো? বেশ!" ওঁর রসিকতায় কেউ আঘাত পেত বলে মনে হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, অমন নির্মল আত্মার মানুষ আর দেখেছি বলে মনে হয় না।
জ্যোতিরিন্দ্র ছিলেন সুশ্রী পুরুষ, ভাসা আয়ত চোখ, সুন্দর কালো দীর্ঘ ভ্রূ, টিকালো নাক, ব্যাকব্রাশ চুল। মানুষটিকে দেখে অতি অল্পবয়সেই আমার মনে হয়েছিল, যাদের আমি অহরহ দেখি, এই মানুষটি সেই তথাকথিত দলের মানুষ নন। ইনি অন্য জগতের মানুষ। সম্ভ্রান্ত সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের মানুষ ছিলেন তিনি। ওই সামন্ততান্ত্রিকতার একটুও স্পর্শ লাগেনি ওঁর গায়ে বা ওঁর স্বভাবে; জীবনদর্শনে এমনকী জীবনযাত্রায়। ওঁর জন্মবীজই ছিল ধ্যানীর। এবং ছিলেন সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মানুষ। কাউকে তোষামোদ করা ওঁর ধাতে ছিল না। ফলে ওঁর রবীন্দ্রসংগীতের একটিও ক্যাসেট নেই। ডিস্ক রেকর্ড ছিল কি না বলতে পারব না। ওঁর মেয়ে-জামাইয়ের উদ্যোগে ওঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'মধুবংশীর গলি' ও অন্যান্য রচনার সিডি বেরুচ্ছে। তার মধ্যে কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের সি.ডি.-র উল্লেখ দেখলাম না। শুনেছি ওঁর ঘনিষ্ঠ কবিবন্ধু বিষ্ণু দে-র বাড়িতে নাকি ওঁর রবীন্দ্রসংগীতের বহু রেকডিং করা আছে।
বটুক মেসোমশাই কতটা সূক্ষ্ম সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ মানুষ ছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। একবার দুপুরবেলা মামণির কাছে ওঁর খাওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ দোতলায় আমার ঘরে ঢুকে আমার স্ত্রীকে বললেন: "বাঃ, সুন্দর ঘরটি তো তোমাদের। ওই ছবিটি কার?” উত্তরে আমার স্ত্রী: "ছবিটি আমায় ভাইয়ের। ও নেই। গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ডুবে যায়।” বটুক মেসোমশাই একদম চুপ করে গেলেন, একটিও কথা না বলে ঘর ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মামণি ওঁর জন্য খাবার সাজিয়ে বসে আছেন। বটুক কই, বটুক কই, কোথাও উনি নেই। এর ব্যাখ্যা কী?
আর-একটি দৃষ্টান্ত: আমার এক পাড়ারই আবাল্য বন্ধু বিমল মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে। তখন জ্যোতিরিন্দ্র বোখারোতে একটা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। 'উল্কা' নাটক হবে। কলকাতা থেকে বিমলেরা গেছে 'উল্কা' নাটক করতে। জ্যোতিরিন্দ্র নাটকের সংগীত পরিচালক। একদিন বিমলকে ওঁর আস্তানায় নিয়ে গিয়ে উনি নাটকের গানের রিহার্সল দিতে শুরু করলেন। বললেন: "বাঃ বেশ গলা তো তোমার। তোমার একটা পছন্দসই গান শোনাও তো আমাকে।" বিমল একটি ভজন গেয়েছিল। উনি বিমলের কণ্ঠস্বরে একেবারে আপ্লুত। "তুমি গানের চর্চা করো না? চর্চা চালিয়ে যাও।” অদ্ভুত ঘটনা তারপর। প্রায় দু-বছর বাদে বালিগঞ্জ প্লেসে বিমলের বাড়ির উলটো দিকের বাড়ির রোয়াকে বসে 'বিমল বিমল' বলে ডাকাডাকি শুরু করলেন। বারান্দায় বেরিয়ে এসে বিমল দেখে বটুকদা। নীচে নেমে আসতেই উনি বললেন, "চলো তোমার বাড়িতে। ওই যে ভজনটি তুমি গেয়েছিলে সেটি আবার শুনব বলে এসেছি।" বিমল গাইল। "ভারি সুন্দর গলা তোমার। গানটা ছেড়ো না।" বিমল কে? আমার মতোই সাধারণ মানুষ। হ্যাঁ, ভালো গাইতে পারে। দু-বছর পরেও বটুক মেসোমশাই ভুলতে পারেননি, মনে করেছেন- এইরকম গুণসম্পন্ন ছেলেটিকে উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজন। তাই এসেছেন ওর কাছে। হয়তো তা-ও নয়, সংগীত-আত্মার মানুষ বলেই জ্যোতিরিন্দ্র সেদিন বিমলের বাড়িতে উপস্থিত। একটা অলঙ্ঘনীয় টান। একধরনের উন্মাদনা- যেখানে কোনো পাটোয়ারি হিসেবের নামগন্ধ নেই।
সূক্ষ্মতারে বাঁধা মানুষটির গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ইন্দিরা গান্ধি তখন বোধ হয় কেন্দ্রের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী অথবা প্রধানমন্ত্রীও হতে পারেন, জ্যোতিরিন্দ্রকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলেছিলেন- "প্রয়োজন হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।" ঘটনাটি ঘটে শান্তিনিকেতনে। তখন এমনিতেই বটুক মেসোমশাইয়ের
অর্থকষ্ট চলছে। সবাই বলছে, স্ত্রী বার বার বলছেন, ইন্দিরা গান্ধিকে একবার জানাতে। সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না তিনি। সকলের জোরাজুরিতে শেষপর্যন্ত উনি চিঠি দিলেন। পত্রপাঠ ইন্দিরা গান্ধির উত্তর- সপরিবারে দিল্লি চলে আসার অনুরোধ।
দিল্লির রামলীলা অনুষ্ঠানের মস্ত ভার দিলেন ইন্দিরা জ্যোতিরিন্দ্রের উপর। বেশ জমজমাট অনুষ্ঠান হয়ে উঠল ওঁর পরিচালনায়। এইখানেই ওঁর মুখে শোনা একটি অলৌকিক ঘটনা। আমরা জানি, যেখানে রামনাম হয়, সেখানেই শ্রীহনুমান উপস্থিত থাকেন। জ্যোতিরিন্দ্র লক্ষ করেছিলেন, ধুতিপাঞ্জাবি পরিহিত একজন শক্তসমর্থ মানুষ প্রতিদিন সকলের শেষে শেষ সারিতে বসে গম্ভীরভাবে রামগান শুনে সকলের ওঠার আগেই মাঠের অন্ধকারে মিশে যান। একদিন জ্যোতিরিন্দ্র ওঁকে অনুসরণ করেন। হঠাৎ মানুষটি পিছন ফিরে, ক্রোধোদ্দীপ্ত স্বরে- "কী চাই আপনার, কোনো কথা নয় ফিরে যান।" বটুক মেসোমশাই কোনো উত্তর দিতে পারেননি। বুঝলেন শুধু ওঁর শ্রীহনুমানজীর দর্শন হয়েছে। ওঁর নিজের মুখেই শোনা।
দুঃখের বিষয়, এবং লজ্জারও, আমরা বাঙালিরা গুণীকে চিনতে পারি না। চিনলেও গুণের মর্যাদা দিতে ভুলে গেছি। আগেও, এখনও, যে-মানুষ উপেক্ষিত, তিনি উপেক্ষিতই থাকেন। মৃত্যুর পরেও তাঁর বিশেষ পরিবর্তন হয় না।
বটুক মেসোমশাই কথঞ্চিৎ খামখেয়ালি মানুষ ছিলেন। একথাও সত্য তবে যে-কাজে তিনি হাত দিতেন একটা ধর্মীয় উন্মাদনা নিয়ে সে-কাজে ডুবে যেতেন। গণনাট্যের সময়ে যা দেখা গিয়েছে, যখন আসানসোলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে ওখানেই থাকতেন, তখনও তিনি সেই একই মানুষ। উর্মিলা মাসি যতদিন জীবিত ছিলেন, সুখে-দুঃখে ওই ভদ্রমহিলা সর্বদা স্বামীর পাশে। স্বামীর যেকোনো কাজে বা ইচ্ছেয়, যা অন্যের চোখে পাগলামি বলে মনে হতে পারে- উর্মিলা মাসির উৎসাহ কিন্তু বটুক মেসোমশাই পেয়ে গেছেন। প্রকৃত অর্থে সহধর্মিনী। এইটিই বোধ হয় বটুক মেসোমশাইয়ের জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মরুদ্যান ছিল।
আমার সাহিত্যিক বন্ধু, বর্তমানে প্রয়াত, সুশীল সিংহ- এঁর স্ত্রী শান্তাদি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কাছে গান শিখতেন। ওঁর মুখেই শুনেছি জ্যোতিরিন্দ্র পাখি-বিশেষজ্ঞও ছিলেন। আসানসোলে থাকতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভোরবেলায় ঘুম থেকে তুলতেন। বাইনোকুলার হাতে বলতেন চলো, আমার সঙ্গে, কতরকম নতুন পাখি দেখবে, চলো। ওই দেখো, এইটি অমুক পাখি, এ পাখি এখানকার
নয়, দুমকা হাজারিবাগের জঙ্গলে দেখা যায়। এর রঙটা দেখো, ডাক শুনলে তো মোহিত হয়ে যাবে। পাখিটার জাত গোত্র, আঞ্চলিক নাম পর্যন্ত বলে দিতেন। এই পক্ষী-অন্বেষণ বা একধরণের ঐশী উন্মাদনা চলত সকাল আটটা অবধি। তবে এই সমস্ত কাজই উনি করতেন এক নির্বন্ধন ভালোবাসার টানে। যেখানে যখন চাকরি করতেন, সেই স্কুলেরই নয়, সেই শহরের মানুষজনও ওঁর বন্ধু হয়ে যেত। কিন্তু একনাগাড়ে কোনো কাজ বেশিদিন করতে পারতেন না। কোনো মনোমালিন্য নয়, মনোমালিন্য হবার সুযোগই দিতেন না উনি।
প্রকৃত অর্থে উনি একজন সংবেদনশীল গোত্রের মানুষ ছিলেন, কারুর একটা কথা বা মুখভঙ্গিতে বুঝে যেতেন, এইখানে তাঁর প্রয়োজনীয়তা শেষ। পাততাড়ি গোটাতে হবে। এবারে অন্যত্র, অন্য কোথাও। রাজনৈতিক বিশ্বাসে উনি সম্পূর্ণ কম্যুনিস্ট, ভেজাল নন। কিন্তু জমিদার বংশের ছেলে, কোথাও যেন একটা সংকোচ, সারাজীবন অর্থকষ্টে ভুগেছেন, সেইভাবে কারুর কাছে মুখ ফুটে বলতে পারেননি- না তার শিল্পকর্মের জন্য, না তাঁর পারিবারিক দুর্দশার কথা ভেবে।
'ইগো' শব্দটি এখানে খাটে না, বলা উচিত আত্মসম্ভ্রমবোধ। জীবদ্দশায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কোনোদিন অর্থকষ্ট লাঘব হতে শুনিনি। বোধ হয় সেই আত্মসন্ত্রবোধের তাড়নায় সদাই তিনি পীড়িত থাকতেন। জানি না, শিল্পীর মন জটজটিলতায় দুর্গম কি না। সেখানে বোধ হয় কারুর প্রবেশাধিকার নেই।
শেষের দিকে 'পাঠ-ভবন'-এ শিক্ষকতা পর্বে, ওঁকে মনে হত বড়োই যেন অনিকেত। উর্মিলা মাসি ইহজগতে নেই। এইসব প্রতিভা সংরক্ষণযোগ্য। তার জন্য চাই সমমনস্কতার সংবেদনশীল রক্ষকের। শেষপর্যন্ত তিনি রক্ষকহীন হয়ে পড়েছিলেন। সংসার-সমাজ তাঁকে অপমান দিয়েছে, সম্মান পেয়েছেন তুলনায় সামান্য।
ফলে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের যে প্রতিভার বিচ্ছুরণ আমরা দেখেছি, তা তাঁর সমগ্র প্রতিভার হিমশৈলের চূড়ামাত্র। তাঁর উপযুক্ত উত্তরসূরী নেই। ছেলের কর্মস্থল চেন্নাই। সেখান থেকে একাই জ্যোতিরিন্দ্র ফিরছিলেন কলকাতায় করমণ্ডল এক্সপ্রেসে। ট্রেনেই 'ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক' এবং মৃত্যু। এক মহাপ্রতিভাধরের মরদেহ, বেওয়ারিশ লাশ হয়ে জমাদারদের ময়লাফেলার গাড়িতে তখন। লাশ শনাক্ত হল বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ময়লা ফেলার গাড়িতে উপেক্ষার জীবনাবসান। আমাকে কেন, আপামর শিক্ষিত বাঙালির কাছে, নিশ্চয়ই কষ্টদায়ক, পীড়াদায়ক। সবচেয়ে বড়ো কথা বাঙালির এইটি জাতীয় লজ্জা।
সূত্র : গদ্য সগ্রহ ২ || তবুও প্রয়াস

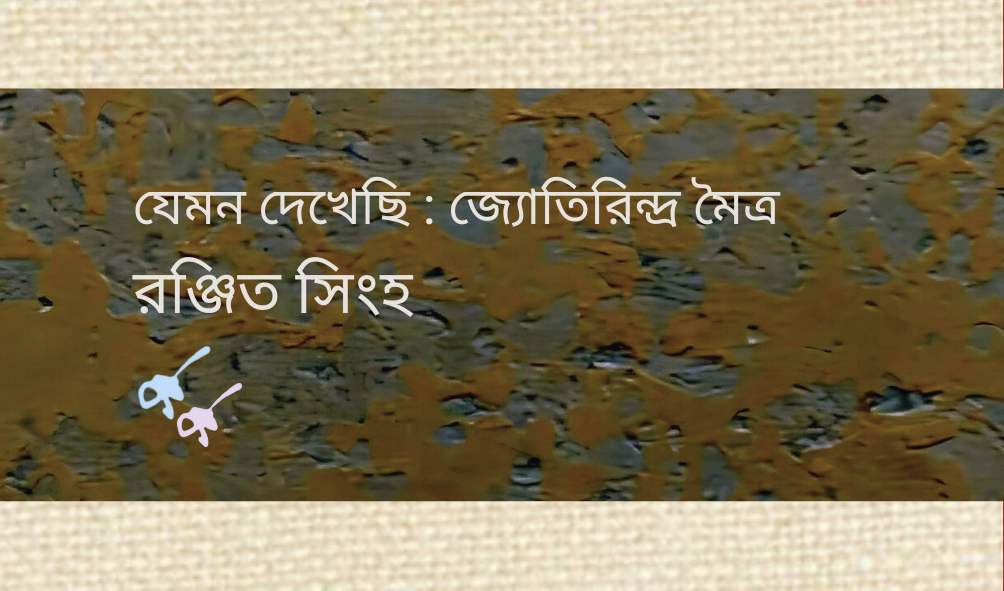
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন